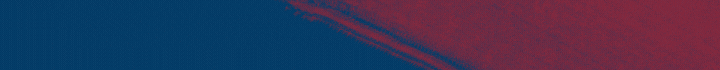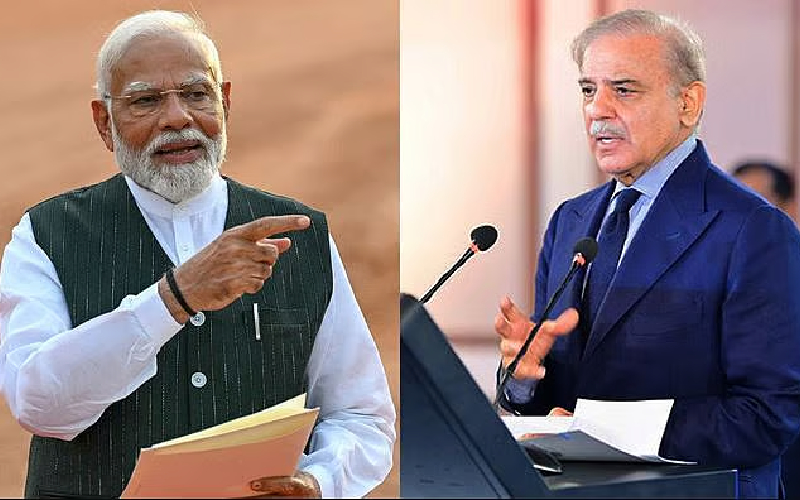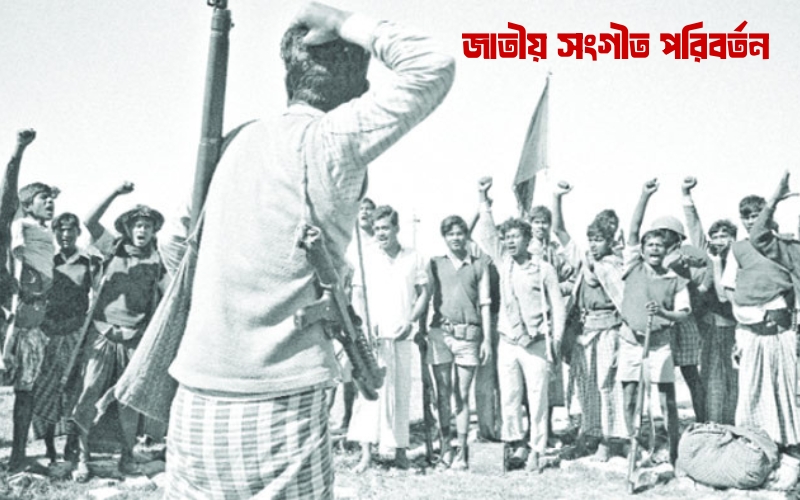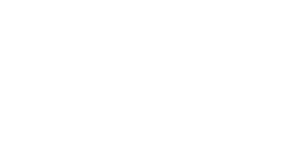সমাজে প্রায়শই আমরা কিছু ধারণার মোহবশত কাউকে শ্রেণিবদ্ধ করে ফেলি—একজন রিকশাওয়ালাকে গরীব, একজন সুশিক্ষিত শহুরে ব্যক্তিকে সফল। কিন্তু কি আছে সত্যের মূল্যায়নে? সম্প্রতি একটি আলোচনায় মাসে ৩০ হাজার টাকা রোজগার করা রিকশাওয়ালাদের গরীব হওয়ার সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই রোজগার দেশের জিডিপি প্রতি মানুষের চেয়েও বেশি, তবু আমরা তাদের গরীব ভাবি কেন? এই প্রবন্ধে আমি এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করব—আমাদের মানসিকতা, সামাজিক বিচার, এবং নিজেদের ও অন্যদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।
রিকশাওয়ালা, গরীবতার স্টিরিওটাইপ
আমাদের সমাজে রিকশাওয়ালা শব্দটির সঙ্গে গরীবতার ছবি জড়িয়ে আছে। আমরা তাদের কল্পনা করি—ছেঁড়া লুঙ্গি, কালো মুখ, লেখাপড়া জানে না, গ্রাম্য ভাষায় কথা বলে। কিন্তু এই ছবিটি কি সত্যের পুরো অংশ? বর্তমানে রিকশাওয়ালারা মাসে ৩০ হাজার টাকা বা তার বেশি রোজগার করছেন। বাংলাদেশের ২০২৫ সালের জিডিপি প্রতি মানুষের (পার ক্যাপিটা) আনুমানিক ২৮-৩০ হাজার টাকা হওয়ার কথা আছে, যা বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী গণনা করা হয়। এমনিতে এই আয় যথেষ্ট, তবু আমরা তাদের গরীব ভাবি। কেন? কারণ আমাদের মনে একটি স্টিরিওটাইপ গেঁথে আছে—রিকশাওয়ালা মানেই গরীব।
এই ধারণা তাদের পরিধান, চেহারা, এবং ভাষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ছেঁড়া লুঙ্গি পরা রিকশাওয়ালার ছবি আমাদের মনে এমনভাবে বসে যায় যে, তাদের আর্থিক অবস্থা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তোলাই বন্ধ করে দিই। তবে, বাস্তবে অনেক রিকশাওয়ালা নিজেদের পরিবারের জন্য বাড়ি তৈরি করেছেন, সন্তানদের পড়াশোনায় টাকা খরচ করছেন, এমনকি কিছু পরিবারে একাধিক রিকশা কিনে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তাদের শ্রমের মূল্য এবং আয়ের পরিমাণ আমাদের এই স্টিরিওটাইপকে ভাঙতে বাধ্য করে।
আমাদের গরীবতা, মানসিকতার দারিদ্র্য
একইভাবে, আমরা নিজেদের গরীব ভাবতে চাই না। যিনি মাসে ১৫ হাজার টাকা রোজগার করেন, তিনি তাঁকে গরীব বলে মনে করেন না। তার কারণ, তিনি ফিটফাট জামাকাপড় পরেন, শিক্ষিত, শহুরে ভাষায় কথা বলেন, এবং স্মার্ট মনে হন। এই বাহ্যিক চকচকে চেহারা তাঁর মানসিকতাকে বড়লোকের মতো করে তুলেছে। কিন্তু আয়ের তুলনায় ব্যয় বিবেচনা করলে তার অবস্থা গরীবতার কাছাকাছি। শহরে বাড়ি ভাড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খরচ—এসব তাকে আর্থিকভাবে চাপে ফেলে। তবু তিনি নিজেকে গরীব মনে করেন না, কারণ তাঁর পরিচয়ের সঙ্গে গরীবতা মানায় না।
এই দ্বৈত মানসিকতা আমাদের সমাজে একটি বড় সমস্যা। আমরা রিকশাওয়ালাদের গরীব ভাবি কারণ তাদের চেহারা ও পেশা আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে মেলে। কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে আমরা বাহ্যিক প্রকাশকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করি। এই ভুল ধারণা আমাদের অন্যদের প্রতি অবিচার করে এবং নিজেদের সফলতার মায়ায় ডুবে থাকি।
রিকশাওয়ালাদের সাফল্য
২০২৫ সালে বাংলাদেশে রিকশা চালকদের আয় নিয়ে কিছু গবেষণা চলছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটের মতো বড় শহরে একজন রিকশাওয়ালা দৈনিক ১০০০-১৫০০ টাকা রোজগার করেন। মাসে ৩০ দিন কাজ করলে তাদের আয় ৩০-৪৫ হাজার টাকা হয়। এর থেকে খরচ (রিকশার ভাড়া, খাবার, মেরামত) কাটলে হাতে ২০-৩০ হাজার টাকা থাকে। এই আয় গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী এক সাধারণ পরিবারের চেয়ে বেশি। তাদের এই আয় তাদের গরীব নয়, বরং মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের ক্ষমতা দেয়।
তুলনামূলকভাবে, একজন শহুরে কর্মকর্তা যিনি ২০-২৫ হাজার টাকা মাইনে পান, তিনি ভাড়া, শিক্ষা, ইন্টারনেট খরচে প্রায় সমস্ত টাকা খরচ করে ফেলেন। ফলে, তাদের সঞ্চয় কম, এবং অসুস্থতা বা জরুরি পরিস্থিতিতে তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, রিকশাওয়ালারা আর্থিকভাবে আমাদের চেয়ে স্থিতিশীল। তবু আমরা তাদের গরীব ভাবি, কারণ আমাদের মনে পেশার ভিত্তিতে একটি কঠিন ছাঁচ তৈরি হয়ে গেছে।
সামাজিক বিচার ও মানসিকতার পরিবর্তন
এই ধরনের স্টিরিওটাইপ আমাদের সমাজে একটি বড় অন্যায় করে। রিকশাওয়ালাদের শ্রমের মূল্য আমরা স্বীকার করি না, কারণ তারা আমাদের সংজ্ঞায় “সফল” নয়। কিন্তু তাদের শ্রম আমাদের শহর চালায়—বাজার, অফিস, স্কুলে আমাদের পৌঁছায়। তাদের আয়ের তুলনায় আমাদের জীবনযাপনের মান কতটা স্থিতিশীল, তা আমরা বিবেচনা করি না। এই ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি।
প্রথমে, আমাদের রিকশাওয়ালাদের গরীব ভাবা বন্ধ করতে হবে। তাদের পরিচয় তাদের পেশা বা চেহারায় নয়, তাদের পরিশ্রমে। দ্বিতীয়ত, নিজেদের বড়লোক দেখানোর ভানও বন্ধ করতে হবে। আমরা যদি নিজেদের আর্থিক অবস্থা সত্যিকারের মূল্যায়নে বিচার করি, তাহলে দেখব আমরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে দুর্বল। এই ভারসাম্য তৈরি করলে আমাদের সমাজে অর্ধেক সমস্যা—অবহেলা, অবিচার, অহংকার—নিজে থেকেই কমে যাবে।
সমাধানের পথ
শিক্ষা ও সচেতনতা এই পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি। আমাদের শিক্ষাক্রমে এমন শিক্ষা প্রদান করা উচিত যা পেশার ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করার মানসিকতা ভাঙে। গ্রাম্য ভাষা বা লুঙ্গি পরা মানুষের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। সরকার ও গণমাধ্যমের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ—তাদের রিকশাওয়ালাদের শ্রমের মূল্য প্রচার করতে হবে, তাদের জীবনের সফল গল্প তুলে ধরতে হবে।
একইভাবে, আমাদের নিজেদের জীবনযাপনের মান নিয়ে সত্যিকারের মূল্যায়ন করা জরুরি। আমরা যদি বাহ্যিক প্রকাশের জন্য অতিরিক্ত খরচ করি, তাহলে আমাদের সঞ্চয় কমে যায়। রিকশাওয়ালাদের মতো তারা তাদের আয়ের বেশিরভাগ সঞ্চয়ে রাখে, যা তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা দেয়। আমাদের এই শিক্ষা থেকে নেওয়া উচিত।
সমাজের জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি
রিকশাওয়ালাদের গরীব ভাবা এবং নিজেদের বড়লোক দেখানো আমাদের মানসিকতার দারিদ্র্যের প্রতিফলন। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে শ্রমিক শ্রেণি অর্থনৈতিক চাক্ষুষে অবদান রাখছে, তাদের প্রতি সম্মান দেখানো জরুরি। মাসে ৩০ হাজার টাকা রোজগার করা রিকশাওয়ালা গরীব নয়—তিনি একজন পরিশ্রমী মানুষ, যিনি নিজের পরিবারের জন্য লড়াই করছেন। আমরা যদি এই সত্য গ্রহণ করি এবং নিজেদের ভুল ধারণা ত্যাগ করি, তাহলে সমাজে সমানতা ও শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠবে।
আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে নিজেদের মধ্যে এই পরিবর্তন আনা। রিকশাওয়ালাদের প্রতি সম্মান দেখানো, তাদের শ্রমের মূল্য স্বীকার করা, এবং নিজেদের আর্থিক অবস্থা সত্যিকারের মূল্যায়নে বিচার করা—এই দুটি পদক্ষেপই আমাদের সমাজের অর্ধেক সমস্যার সমাধান করবে। আসুন, আমরা স্টিরিওটাইপ ভেঙে একটি নতুন সমাজ গড়ি, যেখানে প্রতিটি শ্রমের মূল্য আছে, এবং প্রতিটি মানুষের সম্মান রক্ষিত হয়।