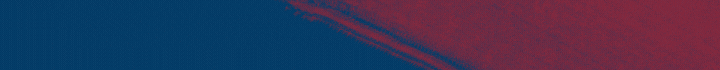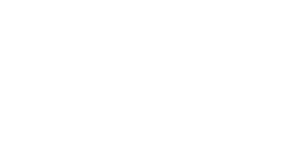গঙ্গার পানির “গড় ৬০% হিস্যা” শব্দবন্ধটি যতটা ভারসাম্যের কথা বলে, বাস্তবে তার প্রতিচ্ছবি ঠিক উল্টো। বর্ষাকালে ভারত বাংলাদেশের দিকে হুড়মুড় করে পানি ছেড়ে দেয়—যেখানে পানির দরকার নেই, সেখানে বন্যা হয়ে যায়। আবার শুষ্ক মৌসুমে, যখন পানি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখন ভারত সেই দরজা প্রায় বন্ধই রাখে। ফলে দুই মৌসুমেই বাংলাদেশ পড়ে বিপদে—একদিকে অতিরিক্ত পানিতে ফসল ভাসে, অন্যদিকে পানির অভাবে ধানক্ষেত ফেটে চৌচির।
এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিতরণ পদ্ধতিই ‘হিস্যার ছকে’ লুকিয়ে থাকা সেই নীরব ফাঁদ, যা বাংলাদেশকে ন্যায্য হিস্যার আশ্বাসে বন্দি করে রেখেছে, অথচ বাস্তবে দেয় একটিমাত্র অপশন—সহ্য করা। চুক্তি অনুযায়ী যৌক্তিকতা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেখানে ভারত শুধু “গড়” পরিসংখ্যান তুলে ধরে দায় এড়িয়ে চলে—ফলে বাংলাদেশের কৃষি, মৎস্য ও দক্ষিণাঞ্চলের পরিবেশ প্রায় প্রতি বছরই পড়ে চরম সংকটে।
চুক্তির কাগজে ৬০%, বাস্তবে কোথাও নেই
১৯৯৬ সালের ৩০ বছরের গঙ্গা পানি চুক্তিতে বলা হয়েছিল, জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত শুকনো মৌসুমে গঙ্গা নদীতে যদি গড় প্রবাহ থাকে ৫০,০০০ কিউসেক, তাহলে বাংলাদেশ পাবে ৬০% অর্থাৎ প্রায় ৩০,০০০ কিউসেক পানি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অন্তত ৪০% সময় ভারত তার প্রতিশ্রুত হিস্যা দেয়নি। বিশেষ করে মার্চ-এপ্রিল মাসে পদ্মা নদী ধু-ধু মাঠে পরিণত হয়। বরেন্দ্রভূমি এলাকায় ধানচাষ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ চুক্তির ভাষায় ‘সহযোগিতা’, ‘ন্যায্যতা’ আর ‘পরিসংখ্যানভিত্তিক বণ্টন’ বারবার উচ্চারিত।
বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দেয়ার ফলে বাংলাদেশের বহু নিচু এলাকা প্লাবিত হয়। অথচ বর্ষায় বাংলাদেশের পানির চাহিদা কম থাকে। চুক্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—সারা বছর গড়ে হিস্যা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু ভারত পানির হিসাব গড়ে নয়, ‘যখন ইচ্ছা তখন’ নীতিতে চালায়, যা চুক্তির চেতনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যার ফলে পদ্মা নদীর পানিপ্রবাহ কমে যায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী অববাহিকায় লবণাক্ততা বেড়ে যায়। নদীর পানি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে নদীনির্ভর মাছের উৎপাদনও মারাত্মকভাবে কমে যায়।
চুক্তিতে “উপলব্ধ পানি” শব্দবন্ধে ভারতের হাত খোলা
চুক্তির একটি মারাত্মক দুর্বলতা হলো—পানি বণ্টনের নিশ্চয়তা নয়, বরং “উপলব্ধ পানি” অনুযায়ী হিস্যা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে ভারত বললেই পারে—“এবার গঙ্গায় কম পানি এসেছে”—আর তাতেই বাংলাদেশ কম পানি পায়। এটি এমন এক কাঠামো, যেখানে দায় নেই, কেবল “উপলব্ধতার” অজুহাত।
যৌথ নদী কমিশন কেবল নামেই যৌথ
চুক্তির আওতায় একটি Joint River Commission (JRC) থাকার কথা ছিল, যারা নিয়মিত বৈঠক করবে, তথ্য বিনিময় করবে, প্রয়োজনে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজবে। কিন্তু বাস্তবে JRC মাঝে মাঝেই নিষ্ক্রিয়। কখনো ভারত সময় দেয় না, কখনো তথ্যই দেয় না। একাধিকবার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চাপ দিলেও ভারতের পক্ষ থেকে তেমন সাড়া মেলেনি।
দক্ষিণ এশিয়ার পানি ভূরাজনীতি
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দক্ষিণ এশিয়ায় পানি এখন আর কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, বরং “কৌশলগত অস্ত্র”। ভারতের মাথার ওপরে চীন, যেখান থেকে ব্রহ্মপুত্র আসে। বাংলাদেশ মাঝখানে পড়ে দ্বিমুখী চাপে। ভারতের আশঙ্কা, চীন ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ বদলে দিতে পারে। আর ভারত এই অনিশ্চয়তায় বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে—পানিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।
২০২৬: নতুন চুক্তি না হলে কী হবে?
১৯৯৬ সালের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে। নতুন চুক্তির আলোচনায় ভারত এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বসেনি। বাংলাদেশ চায়—
- শুষ্ক মৌসুমে সুনির্দিষ্ট পানির নিশ্চয়তা
- যৌথ পরিমাপক ব্যবস্থার কার্যকারিতা
- জরুরি অবস্থায় পানি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা
- সকল নদীর জন্য একটি সমন্বিত বণ্টন কাঠামো।
কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজ্যগুলোর (বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ) রাজনৈতিক চাপ এবং জাতীয় নির্বাচন কেন্দ্রিক কূটনীতি, এই আলোচনার অগ্রগতি ব্যাহত করছে।
বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক যতই ‘অভিন্ন নদীর অভিন্ন বণ্টন’ বলেই ঘোষিত হোক, বাস্তবে এই সম্পর্ক বহুক্ষেত্রেই একমুখী। ফারাক্কা চুক্তির ন্যায্য হিস্যার ছকে ভারত একদিকে আন্তর্জাতিক কূটনীতির সৌজন্য বজায় রাখছে, অন্যদিকে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের নামে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে পানি নিয়ন্ত্রণের একতরফা খেলা। এই পরিস্থিতি শুধু একটি দেশের কৃষি ও পরিবেশ নয়, পুরো অঞ্চলের প্রতিবেশগত ভারসাম্যকে ঝুঁকিতে ফেলছে।
চুক্তির সময়সীমা ২০২৬ সালেই শেষ হচ্ছে। এখনই সময়—বাংলাদেশকে দৃঢ় কূটনৈতিক অবস্থানে গিয়ে, শুধু পরিমাণগত হিস্যা নয়, বরং যৌক্তিক, মৌসুমি প্রয়োজনভিত্তিক, সময়োপযোগী ও বাধ্যতামূলক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন চুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া। নইলে, ‘ন্যায্য হিস্যা’র নামে এই নিষ্ঠুর খেলাটি চলতেই থাকবে—আর বাংলাদেশ হারতেই থাকবে, নিজের নদীতে, নিজের পানিতে।