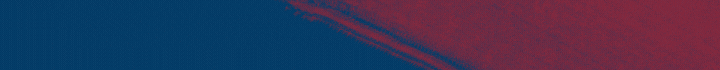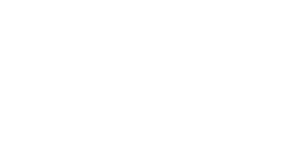পদ্মার বুক শুকিয়ে গেছে। উত্তরাঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে মরুকরণের পদধ্বনি। আর এই সংকটের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক নাম—ফারাক্কা বাঁধ। বাংলাদেশে একে অনেকেই বলেন “মরণ বাঁধ”, কারণ এটি শুধু একটি কংক্রিটের নির্মাণ নয়, বরং একটি জাতির জীবিকাকে পদদলিত করার দীর্ঘশ্বাস।
কীভাবে তৈরি হলো ফারাক্কা বাঁধ
ভারত সরকার কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা ও পলি সরানোর অজুহাতে ১৯৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের ফারাক্কায় নির্মাণ করে ১২৪৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২৩ মিটার উচ্চতার এই বাঁধটি। নির্মাণে ব্যয় হয় ১৫৬ কোটি রুপি। গঙ্গা নদীর উপর নির্মিত এই বাঁধটি চালু হয় ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল। অথচ তার আগেই, ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রকল্প নিয়ে স্বাক্ষর করেন একটি চুক্তি, যা ইতিহাসে ‘মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি’ নামে পরিচিত। চুক্তিতে বলা হয়, ফারাক্কা বাঁধ পুরোপুরি চালু করার আগে ভারত পরীক্ষামূলকভাবে ৪১ দিনের জন্য (২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে, ১৯৭৫) বাঁধ চালু করবে। এই সময়ে ফিডার ক্যানেলের মাধ্যমে প্রতিদিন ১১ থেকে ১৬ হাজার কিউসেক পানি হুগলি নদীতে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।
ভারতের একতরফা পদক্ষেপ
পরীক্ষামূলক ৪১ দিন শেষ হলেও ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন কোনো সমঝোতা ছাড়াই ফিডার ক্যানেল চালু রাখে এবং গঙ্গার পানি নিজ দেশে সরিয়ে নিতে থাকে। ১৯৭৬ সালের শুষ্ক মৌসুমে ভারত একতরফাভাবে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করে নেয়, যা সরাসরি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নদীর প্রবাহ হ্রাস, কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়া এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের সূচনা করে।
ফারাক্কার ধাক্কা: বাংলাদেশে প্রভাব
-
পদ্মা ও অন্যান্য নদীর প্রবাহ ভয়াবহভাবে কমে যায়
-
উত্তরাঞ্চলে খরা, ধানের উৎপাদনে ধস
-
ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নেমে যায়
-
মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হয়
-
উপকূলেও লবণাক্ততা বাড়ে
ফারাক্কা চুক্তির পাঁচ দশক: প্রতিশ্রুতি আছে, বাস্তবায়ন কোথায়?
ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে চুক্তির ইতিহাস দীর্ঘ, কাগজে-কলমে সমঝোতার পর সমঝোতা হলেও বাস্তব চিত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রতি অবিচারই রয়ে গেছে স্থায়ী। ১৯৭২ সালে যৌথ নদী কমিশন (Joint Rivers Commission) গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্তবর্তী নদীগুলোর পানি বণ্টন প্রশ্নে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে হয় ঐতিহাসিক ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি। চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল—ফারাক্কা বাঁধ চালুর আগে দুই দেশের মধ্যে পানির ভাগ নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছানো। তবে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা ফিডার ক্যানেল পরে একতরফাভাবে স্থায়ীভাবে ব্যবহার শুরু করে ভারত।
১৯৭৭ সালের চুক্তি: প্রথম পানি ভাগাভাগির কাঠামো
চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়—
১. বাংলাদেশ পাবে গড় পানির ৬০% হিস্যা
২. শুকনা মৌসুমে ১০ দিন পরপর সার্কেল হিসাব করে বাংলাদেশ পাবে ৩৪,৫০০ কিউসেক পানি, আর ভারত পাবে ২০,৫০০ কিউসেক।
৩. বাংলাদেশের প্রাপ্ত পানি কখনোই তার হিস্যার ৮০% এর নিচে নামবে না।
কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বহু সময়ই বাংলাদেশ এর চেয়ে অনেক কম পানি পেয়েছে, যা ছিল চুক্তি লঙ্ঘনের স্পষ্ট নিদর্শন।
পরবর্তী সমঝোতা: মেয়াদি কিন্তু দুর্বল প্রয়োগ
-
১৯৮২ সালের অক্টোবরে হয় ২ বছর মেয়াদী একটি সমঝোতা স্মারক।
-
১৯৮৫ সালের নভেম্বরে হয় ৩ বছর মেয়াদি আরেকটি চুক্তি (১৯৮৬–৮৮)।
এই চুক্তিগুলো ছিল স্বল্পমেয়াদি ও কার্যকর নজরদারি ছাড়া। ফলে ভারত প্রায়ই চুক্তির শর্ত ভেঙে পানি প্রত্যাহার করে নেয়।
১৯৯৬ সালের ৩০ বছরের চুক্তি: নতুন আশার আলো?
১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবগৌড়া একটি ৩০ বছরের পানি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
মূল শর্ত:
-
১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত শুকনা মৌসুমে গঙ্গার পানি দুই দেশ ভাগ করে নেবে
-
ভারত গঙ্গার প্রবাহ গত ৪০ বছরের গড় মাত্রা বজায় রাখার চেষ্টা করবে
-
বাংলাদেশ অন্তত ৩৫,০০০ কিউসেক পানি পাবে সংকটময় পরিস্থিতিতেও
কিন্তু বাস্তবতা হলো—এই চুক্তির অধীনেও ভারত বহুবার বাংলাদেশকে নির্ধারিত হিস্যার কম পানি দিয়েছে, কখনো কখনো মাত্র ১৫–২০ হাজার কিউসেক, যা কৃষি ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি।
আন্তর্জাতিক নদী আইন কি বলছে?
আন্তর্জাতিক নদী ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী, উজানের দেশ কখনোই নিজের সুবিধায় ভাটির দেশের ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু ভারত বারবার গঙ্গার পানি আটকে রেখে বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষি, পরিবেশ ও জ্বালানি খাতকে বিপন্ন করে তুলেছে।
বাংলাদেশের করণীয়: কৌশলগত রূপরেখা
১️জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা
ফারাক্কার অশুভ প্রভাব রোধে রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে সরকার, বিরোধী দল ও বুদ্ধিজীবীদের একযোগে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এটি কেবল পরিবেশগত নয়, একটি জাতীয় নিরাপত্তা ও টিকে থাকার প্রশ্ন।
আন্তর্জাতিক জনমত গঠন
বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।
আঞ্চলিক পানি সহযোগিতা
চীন, ভারত, নেপাল ও ভুটানসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক সমঝোতায় পৌঁছাতে ‘আঞ্চলিক নদী কমিশন’ গঠন সময়ের দাবি। এটি নদীর পানি ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে পারে।
ভারতের ওপর কূটনৈতিক চাপ
ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বন্ধে দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে। কারণ এসব প্রকল্প ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পানিপ্রাপ্তিকে আরও বিপন্ন করতে পারে।
কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার
মেকং নদী কমিশনের আদলে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী কূটনৈতিক কাঠামো গড়তে পারে, যা নদী ভাগাভাগির সুষ্ঠু দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে।
গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ
দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী ও বাস্তবসম্মত সমঝোতা চুক্তি করতে হবে যাতে গঙ্গার পানি প্রবাহ ভবিষ্যতে বাধাগ্রস্ত না হয়।
অন্যান্য বাঁধ প্রকল্পের বিরোধিতা
ফারাক্কার পাশাপাশি গজলডোবা ও টিপাইমুখ বাঁধের বিরুদ্ধেও তৎপরতা চালানো জরুরি। এগুলোর নির্মাণ ও পরিচালনা বাংলাদেশের নদী ও কৃষির উপর সমানভাবে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলছে।
মিডিয়া ও জনসচেতনতা
সরকারি ও বেসরকারি প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ফারাক্কা সংকট নিয়ে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তুলতে হবে।